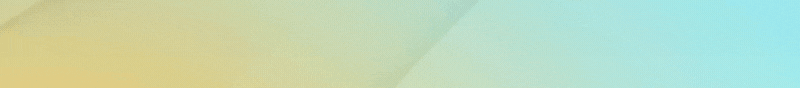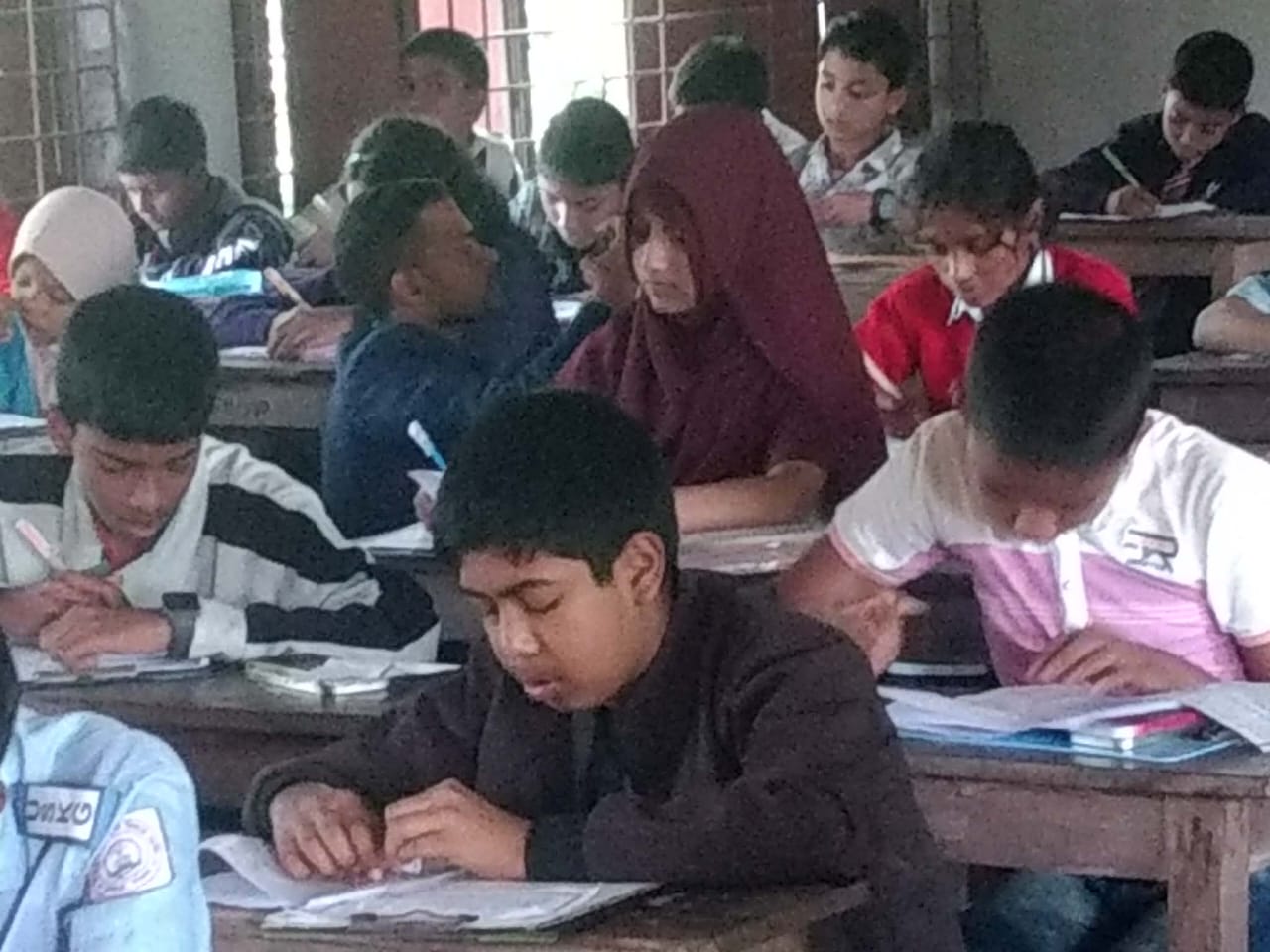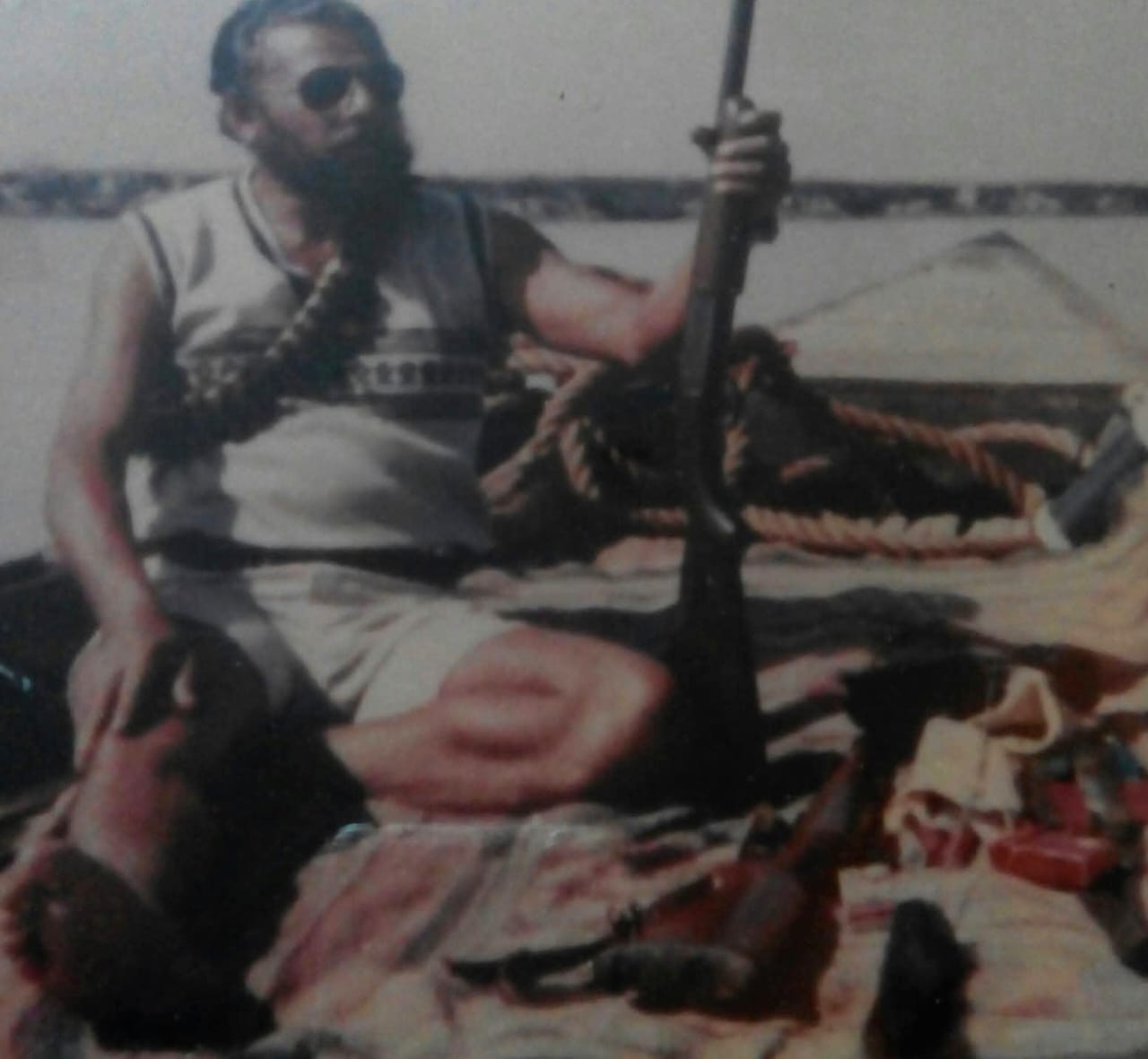আন্দোলন-সংগ্রামে সরকারি, বেসরকারি সম্পদ ধ্বংসের অর্থ নিজের সম্পদ নষ্ট করা ! মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাঃ
- প্রকাশিত: বুধবার, ২৯ অক্টোবর, ২০২৫
- ১৪০ বার পড়া হয়েছে

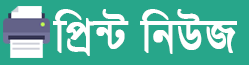
ড. আব্দুল ওয়াদুদ.
আন্দোলন ও সংগ্রাম একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। মানুষ রাষ্ট্রীয় অন্যায়, অবিচার, দমন–পীড়নের বিরুদ্ধে নিজেদের দাবি আদায়ে আন্দোলন করে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে দেখা যায়, এসব আন্দোলনের সময় অনেকেই রাস্তায় গাড়ি পোড়ায়, সরকারি ভবন ভাঙচুর করে, রেললাইন উপড়ে ফেলে, এমনকি সাধারণ মানুষের সম্পদ, দোকানপাটেও আগুন দেয়। এতে রাষ্ট্রের সম্পদ ধ্বংস হয়, দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জনগণের কষ্ট বাড়ে।
এ প্রশ্ন জাগে — মানুষ যদি নিজের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করে, তবে কেন নিজের দেশের সম্পদই ধ্বংস করে? এর মূল কারণ কেবল রাজনৈতিক নয়, গভীরভাবে এটি মনোবৈজ্ঞানিক আচরণগত সমস্যা।
মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা:
১️। জনসমষ্টির মানসিকতা (Crowd Psychology):
একজন ব্যক্তি একা থাকলে যুক্তিসঙ্গতভাবে চিন্তা করে, কিন্তু যখন সে জনসমুদ্রের অংশ হয়, তখন তার ব্যক্তিগত বুদ্ধিবোধ অনেক সময় হারিয়ে যায় মনোবিজ্ঞানী গুস্তাভ লে বঁন (Gustave Le Bon) বলেছেন,
”Crowd makes individuals irrational” অর্থাৎ, জনতার মধ্যে ব্যক্তিগত চেতনা হারিয়ে যায়। আবেগ, রাগ, প্রতিশোধ – এসবই তখন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এককভাবে শান্ত প্রকৃতির মানুষও ভিড়ের মধ্যে ধ্বংসাত্মক হয়ে ওঠে।
২️। বঞ্চনা ও হতাশার প্রতিক্রিয়া (Frustration–Aggression Theory):
মানুষ যখন দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত, অবহেলিত বা নিপীড়িত থাকে, তখন তার মধ্যে জমে থাকা ক্ষোভ একসময় সহিংস রূপ নেয়।
মনোবিজ্ঞানী Dollard ও তার সহকর্মীরা বলেছেন-
“Frustration always leads to aggression”
অর্থাৎ, দীর্ঘ বঞ্চনা ও অবিচারের প্রতিক্রিয়ায় মানুষ প্রতিশোধমূলক আচরণ করে। আন্দোলনের সময় সেই ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে সরকারি সম্পদ বা প্রতীকী শত্রুর ওপর।
৩️। প্রতীকী প্রতিশোধ (Symbolic Revenge):
অনেকেই মনে করে, সরকারি ভবন, যানবাহন বা অফিস ধ্বংস করা মানে “সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া”। তারা বুঝতে পারে না, এসব সম্পদ আসলে জনগণেরই সম্পদ। এটা এক ধরনের মানসিক বিভ্রান্তি, যেখানে সরকার ও রাষ্ট্র–এর পার্থক্য মানুষ বুঝতে আন্দোলনকারীরা ব্যর্থ হয়।
৪️। উত্তেজনা ও সংক্রামক আবেগ (Emotional Contagion):
মানুষের আবেগ খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এক-দুইজন আগুন দিলে বা ভাঙচুর শুরু করলে, আশপাশের মানুষও একই আবেগে জড়িয়ে পড়ে। এটি সংক্রামক আচরণ (Contagious Behavior)। তখন যুক্তি কাজ করে না; কাজ করে শুধুই রাগ ও দলীয় উন্মাদনা।
৫️। শিক্ষার অভাব ও নাগরিক চেতনার ঘাটতি:
যেখানে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব, সেখানে আন্দোলন হয় আবেগনির্ভর, যুক্তিনির্ভর নয়। মানুষ যদি জানত, “সরকারি সম্পত্তি মানেই আমার সম্পত্তি,” তাহলে এমন ধ্বংসাত্মক প্রবণতা অনেক কমে যেত।
এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার উপায়-
ক) রাজনৈতিক ও নাগরিক শিক্ষা:
স্কুল–কলেজ পর্যায়ে নাগরিক দায়িত্ব, আন্দোলনের নৈতিকতা ও অহিংস প্রতিবাদের শিক্ষা থাকা জরুরি।
খ) নেতৃত্বের দায়িত্ব:
দলের নেতা-কর্মীরা যেন আন্দোলনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখেন এবং সহিংসতা নিরুৎসাহিত করেন।
গ) আইনের কঠোর প্রয়োগ:
যে কেউ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করবে, তার বিরুদ্ধে দ্রুত বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
ঘ) মনোবৈজ্ঞানিক পরামর্শ ও সচেতনতা:
যুব সমাজের মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের মানসিক প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।
রাষ্ট্র আমাদের সবার — তার সম্পদ, ভবন, যানবাহন, সেতু সবই জনগণের অর্থে তৈরি। এগুলো ধ্বংস মানে নিজের ঘর ধ্বংস করা।
ধ্বংসকারী বুঝতে পারে না এই সম্পদে তারও অধিকার ও অংশীদারিত্ব রয়েছে। জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় এই সম্পদ গড়ে তোলা হয়। দেশের প্রতিটা নাগরিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর দিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করে।
আন্দোলন তখনই সফল হয়, যখন তা গঠনমূলক ও অহিংস থাকে। দেশের স্বার্থে, নিজের স্বার্থে— আমাদের শিখতে হবে কিভাবে দাবি আদায় করতে হয় অন্যের ক্ষতি না করে, নিজের দেশের ক্ষতি না করে। আবেগ নয় যুক্তি দিয়ে আন্দোলন করতে হবে। সরকারি সম্পদ মানেই জনগণের সম্পদ।
ধ্বংস নয়, সচেতনতা ও নৈতিকতার মাধ্যমে পরিবর্তন আনাই প্রকৃত সংগ্রাম।
ড. আব্দুল ওয়াদুদ
ফিকামলী তত্ত্বের জনক,
মনোবিজ্ঞান গবেষক, রাজনৈতিক বিশ্লেষক।