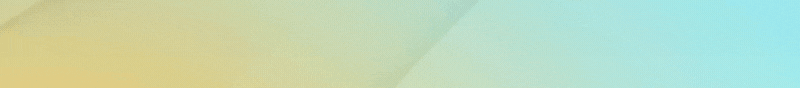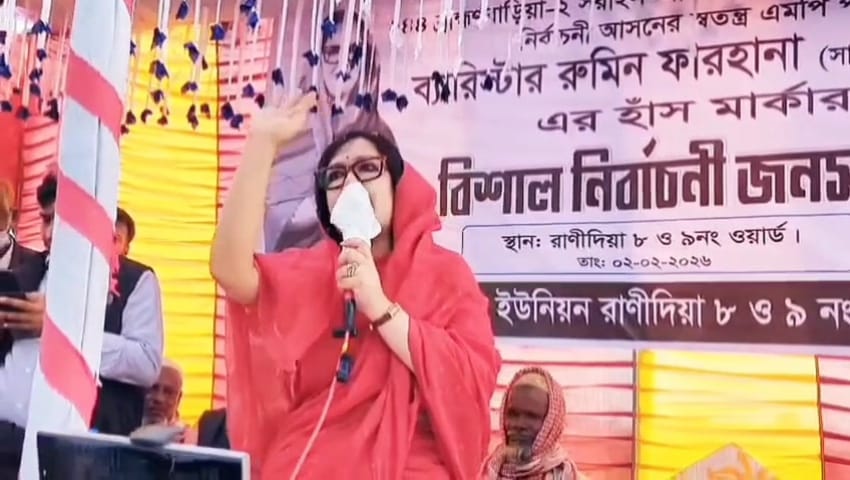পিআর পদ্ধতিতে কেমন আছে নেপাল
- প্রকাশিত: বুধবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৫
- ১৫৩ বার পড়া হয়েছে

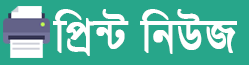
ভোলা প্রতিনিধিঃ
দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, কোনো একক দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম সিপিএন (মাওবাদী কেন্দ্র) ও সিপিএন (ইউএমএল)-এর একত্রীকরণের ফলে গঠিত দলীয় ঐক্য, যার মাধ্যমে একবার সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার গঠন করা সম্ভব হয়। কিন্তু এটি নির্বাচনী ফলাফলের কারণে নয়, বরং দলীয় একত্রীকরণের ফলস্বরূপ। সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে সরকার গঠনে রাজনৈতিক দলগুলোকে জোট গঠন করতে হয়। কিন্তু বারবার জোট গঠন ও ভাঙনের ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, যা সরকার পরিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে ত্বরান্বিত করে। অনেকে এ রাজনৈতিক অস্থিরতার পেছনে বিদ্যমান নির্বাচন ব্যবস্থাকেই দায়ী করেন। ২০১৫ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশটিতে সাতবার সরকার ও প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তন হয়। প্রধানমন্ত্রীদের তালিকা ও মেয়াদকাল বিশ্লেষণে দেখা যায়:
সুশীল কৈরালা: ২০১৪-অক্টোবর ২০১৫, খড়গপ্রসাদ শর্মা গুলি: ১২ অক্টোবর ২০১৫ থেকে ৪ আগস্ট ২০১৬, পুষ্পকমল দাহাল প্রচণ্ড: ৪ আগস্ট ২০১৬ থেকে ৭ জুন ২০১৭, শের বাহাদুর দেউবা: ৭ জুন ২০১৭ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, খড়াপ্রসাদ শর্মা ওলি (দ্বিতীয় মেয়াদ): ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে ১৩ জুলাই ২০২১, শের বাহাদুর দেউবা (দ্বিতীয় মেয়াদ): ১৩ জুলাই ২০২১ থেকে ২৬ ডিসেম্বর ২০২২, পুষ্পকমল দাহাল প্রচণ্ড: ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে বর্তমানে দায়িত্বে। প্রতিটি সরকার পতনের পেছনে ছিল নানা জটিল কারণ: যেমন রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ বিভক্তি, স্বার্থান্বেষী জোট গঠন ও ভাঙন, আদালতের হস্তক্ষেপ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার জটিল সাংবিধানিক হিসাব। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেশটির রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান নির্বাচন ব্যবস্থার কার্যকারিতা পুনর্মূল্যায়ন করা অত্যন্ত জরুরি বলে অনেক রাজনৈতিক দলের সদস্য ও
সাধারণ মানুষ মনে করেন। বারবার সরকার পরিবর্তন ও অস্থিরতার প্রভাব: নেপালে বারবার সরকার ও প্রধানমন্ত্রী পরিবর্তনের ফলে যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তার বহুমুখী প্রভাব রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে।
১. রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রভাব: প্রায়ই দেখা যায়, রাজনৈতিক
দলগুলো সংসদ সদস্যদের মনোনয়ন তালিকা তৈরির সময় দলের প্রতি অতিমাত্রায় অনুগত, দলে অর্থায়নকারী, ক্ষমতাবান ব্যবসায়ী, দলীয়প্রধানদের আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠদের প্রাধান্য দেয়। ফলে যোগ্য নেতৃত্ব উপেক্ষিত হয় এবং ‘সামাজিক ন্যায়বিচার’ ব্যাহত হয়। মনোনয়নপ্রাপ্তরা নিজেদের দলের কাছে ‘ঋণী’ মনে করে এবং কোনো সিদ্ধান্তে দলকে ‘অগ্রাহ্য’ করতে পারেন না, যার ফলে সংসদ কার্যকর নীতি প্রণয়নে ব্যর্থ হয়। সংসদ সদস্যের তালিকা প্রস্তুতে এমন প্রথার ফলে দলের অভ্যন্তরে অসন্তোষ দেখা দেয়, ফলে একটি দল ভেঙে অঞ্চল ও সম্প্রদায়ভিত্তিক নতুন নতুন দল সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্রসঙ্গত ২০০৮ সালে দেশটিতে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ছিল ৭৫টি, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭৮টিতে।
২. রাষ্ট্রীয় পরিসরে প্রভাব: প্রতিটি নতুন সরকার তাদের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কাজ করে। ফলে পূর্ববর্তী সরকারের নীতির ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না। দীর্ঘমেয়াদি সরকার না থাকায় অনেক নীতি বাস্তবায়ন অসমাপ্ত থেকে যায়। ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের ফলে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সচিব এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে, যেমন পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক রদবদল হয়। এতে প্রশাসনিক কাঠামোয় স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় এবং সরকারের নেয়া কোনো পলিসি চলমান থাকে না। বিচার ব্যবস্থা ও সংবিধানে ঘন ঘন হস্তক্ষেপের ফলে আইনের শাসনের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা দুর্বল হয়।
৩. সমাজজীবনে প্রভাব: ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনের ফলে জনগণ বিশ্বাস হারায়, রাজনৈতিক নেতারাও আস্থা হারায়। ফলে তরুণদের মধ্যে ‘রাজনৈতিক বিমুখতা’ দেখা দেয় এবং মানুষ ভোটদানে নিরুৎসাহিত হয় যা গণতন্ত্রের জন্য হুমকি। আবার ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনে সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়, যার প্রধান ভুক্তভোগী হয় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। অবহেলিত অঞ্চলের জনগণ মনে করে তাদের দাবি উপেক্ষিত হচ্ছে, ফলে আঞ্চলিক অসন্তোষ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও আন্দোলনের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।
৪. অর্থনৈতিক প্রভাব: রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীরা আস্থা হারান। ফলে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) হ্রাস পায়। সরকার পরিবর্তনের কারণে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প বাতিল বা স্থগিত হয়। রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাবে রাজস্ব সংগ্রহ বিঘ্নিত হয়। ফলে সরকার ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়। বিনিয়োগ ও রাজস্বপ্রবাহ কমে যাওয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না। দেশটিতে বেকারত্ব বাড়ে এবং অনেক তরুণ বিদেশে পাড়ি দেয়, এতে রেমিট্যান্স-নির্ভরতা বাড়ে। তাছাড়া স্বল্পমেয়াদি সরকারে টেন্ডার ও প্রকল্পের নামে দুর্নীতির প্রবণতা বাড়ে যা রাজনৈতিক বিবেচনায় বরাদ্দ দেয়া হয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে বর্তমান মিশ্র নির্বাচনী ব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। ২০১৫ সালের সংবিধানে নিম্নকক্ষের জন্য ন্যূনতম ভোটপ্রাপ্তির শর্ত (থ্রেশহোল্ড) ছিল ৩ শতাংশ এবং জাতীয় পরিষদের জন্য দেড় শতাংশ। তবে সাম্প্রতিক সময়ে অনেক রাজনৈতিক দল মনে করছে, বারবার সরকার পরিবর্তন ঠেকাতে এবং সরকার গঠনে স্থিতিশীলতা আনার লক্ষ্যে এ থ্রেশহোল্ড বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করা জরুরি।